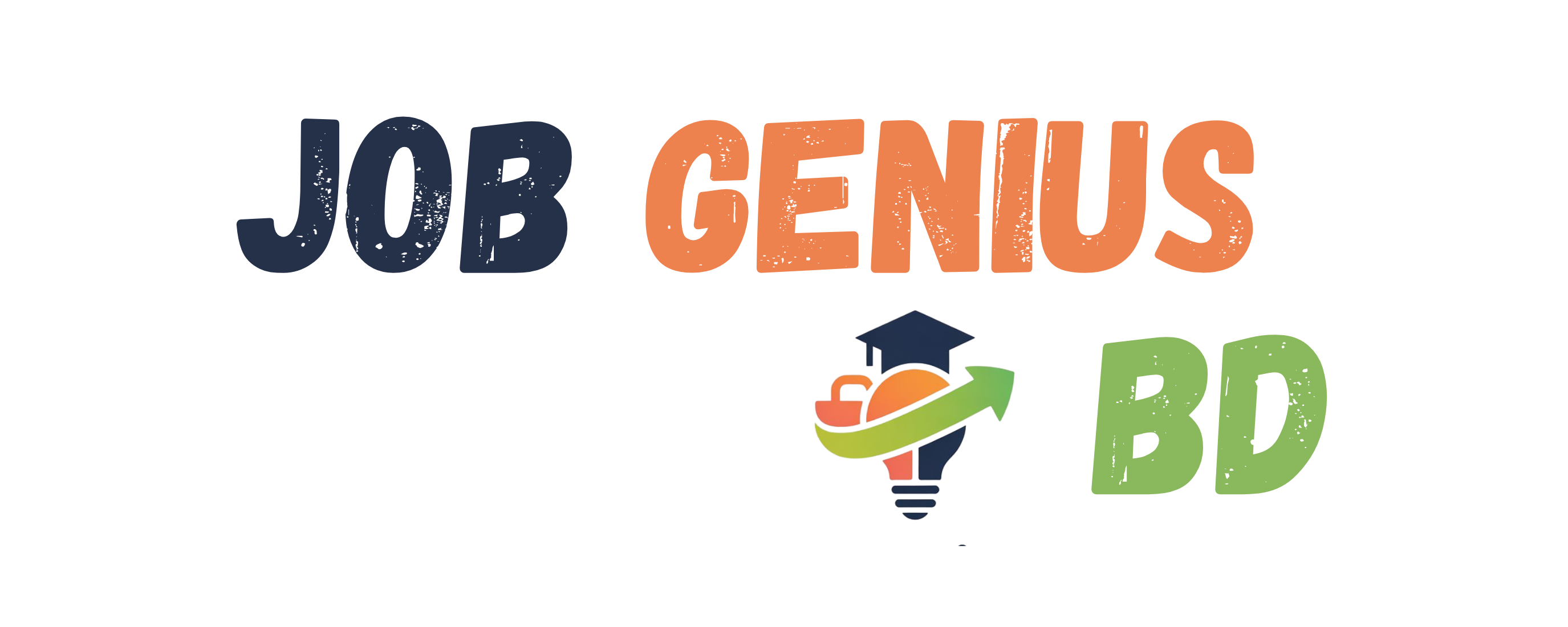📘 Suggestion Details
📜 Title
ধ্বনি, বর্ণ ধ্বণি পরিবর্তন
💡 Explanation
☞ বাগযন্ত্র
একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি । আমরা গান গাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করি। এদের কাজ কি? নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরনের সুরযুক্ত আওয়াজ তৈরি করা। এর মধ্যে রয়েছে ঢোল,তবলা,গিটার,একতারা,বাঁশি ইত্যাদি। প্রত্যেকটি যন্ত্রই অনেকগুলো উপকরণ দিয়ে তৈরি। একটা যন্ত্র তৈরি করতে প্রয়োজন হতে পারে কাঠ, বাঁশ,তার, ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। তেমনি মানুষের বাগযন্ত্র ও বিভিন্ন উপকরণের সমষ্টি।সৃষ্টিকর্তা আমাদের বাগযন্ত্র স্বরতন্ত্র, কন্ঠ,জিহ্বা,তালু ( মুখের ভিতরের উপরের নরম অংশকেই তালু বলে ), মূর্ধা, ( জিহ্বার আগা ) , ওষ্ঠ ( ঠোট ), দন্ত ( দাঁত ), নাসিকা ( নাক ) দিয়ে তৈরি করেছেন।এই বাগযন্ত্রের কাজ কি? এর কাজ ও বিভিন্ন আওয়াজ তৈরি করা । আমরা আওয়াজ তৈরি করার জন্য নিঃশ্বাসের সাথে বাতাস নেই । সেই বাতাস গিয়ে স্বরতন্ত্রকে আঘাত করে । স্বরতন্ত্র হল একটা পর্দার মত । ভেবে নিতে পারেন এটা ঢোলের পর্দার মত। যার মধ্যে আঘাত করলেই কম্পন সৃষ্টি হয়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন শব্দ বা আওয়াজ তৈরি হয় কম্পন থেকে।স্বরতন্ত্রের সেই আওয়াজকে বাগযন্ত্রের অন্যান্য অংশ দিয়ে আমরা আমাদের ইচ্ছামত আওয়াজ বা শব্দ তৈরি করি। এবার প্রশ্ন সব আওয়াজকেই কি ধ্বনি বা শব্দ বলা যায়? নিশ্চয়ই না । সব ধ্বনিই আওয়াজ কিন্তু আওয়াজই ধ্বনি হতে পারে না ? চলুন জানা যাক ধ্বনি কী?
☞ ধ্বনি ও এর প্রকারভেদ
মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ করা যায়।সব আওয়াজই অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে না। অথবা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ও অনেক আওয়াজ শুনতে পাই।সবগুলো দ্বারাই কি নির্দিষ্ট কোন একটা কিছু বুঝতে পারি? নিশ্চয়ই না।তাই আমরা বলতে পারি মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে।তবে সব আওয়াজকে ধ্বনি বলা যায় না। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি । তবে কয়েকটি ধ্বনি মিলিত হয়ে একটি অর্থ সৃষ্টি করে।ধ্বনির নিজস্ব কোন অর্থ নেই। যেমন মুখে ‘আ” বললাম । এর কি কোন অর্থ হতে পারে?নিশ্চয়ই না । যদি বলি ’আম’ তাহলে অবশ্যই আমরা একটা নির্দিষ্ট ফলকে বুঝতে পারি। এখানে ‘আম’ মূলত কয়েকটি ধ্বনির সমষ্টি। বাক প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষতম মৌলিক অংশ বা একককে ধ্বনিমূল বলা হয়। ধ্বনিই ভাষার মূল ভিত্তি। ধ্বনি মূলত আমরা শুধু উচ্চারণই করতে পারে। ধ্বনি প্রকাশ করার আর কোন উপায় নাই। বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-
স্বরধ্বনি: উচ্চারণের সময় মুখবিবরে বাতাস বাধা পায় না, স্বাধীনভাবে উচ্চারণ করা যায়।
ব্যঞ্জনধ্বনি: উচ্চারণের সময় মুখবিবরের কোথাও না কোথাও বাতাস বাধা পায়, স্বাধীনভাবে উচ্চারণ করা যায় না। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে আবশ্যিকভাবে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে।
উচ্চারণের কাল-পরিমাণ অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে দুইভাগে ভাগ করা যায় যথাঃ হ্রস্বস্বর ৪টি ( অ,ই,উ,ঈ ) এবং দীর্ঘস্বর ৭ টি ( আ,ঈ,ঊ,এ,ঐ,ও,ঔ )
☞ স্বরধ্বনির প্রকারভেদ
⮚ বাংলা স্বরধ্বনি ১১ টি । স্বরধ্বনিকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
মৌলিক স্বর: এ ধ্বনিকে ভেঙে উচ্চারণ করা যায় না বা বিশ্লেষণ করা যায় না। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭ টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ্যা, এ এবং ও। এগুলোকে পূর্ণ স্বরধ্বনিও বলে। ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন ‘এ্যা’ ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।
যৌগিক স্বর: দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বর বা দ্বিস্বর বা সন্ধিস্বর বলে। বাংলায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫ টি। যেমন: অ + এ = অয়, আ + এ = আয় ইত্যাদি।
⮚ উচ্চারণের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে আবার নিম্নোক্তভাবেও ভাগ করা যায়-
পূর্ণস্বরধ্বনিঃ উচ্চারণের সময় পূর্ণভাবে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোই পূর্ণস্বরধ্বনি।
অর্ধস্বরধ্বনিঃ স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না তাদের অর্ধস্বরধ্বনি বলে অথবা যে স্বরধ্বনি নিজে পূর্ণ অক্ষর গঠন করতে পারে না,কিন্তু অক্ষর গঠনে সহায়তা করে তাকে অর্ধ স্বরধ্বনি বলে।পূর্ণ স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনাভাবেই দীর্ঘ করা যায় না।
দ্বিস্বরধ্বনিঃ পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন: অয়, আয় ইত্যাদি।
☞ সংবৃত ও বিবৃত স্বরধ্বনি
সংবৃত: যে স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর সংকুচিত হয় তাকে সংবৃত স্বরধ্বনি বলে।বাংলায় সংবৃত স্বরধ্বনি ২ টি। যথাঃ ই,উ।
বিবৃত: যে স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর বিবৃত বা প্রসারিত হয় তাকে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে।বাংলায় বিবৃত স্বরধ্বনি ২ টি।যথাঃ অ,আ।
☞ উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি
উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
স্বরবর্ণ
উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
স্বরবর্ণ
কন্ঠ বা জিহবামূলীয় বর্ণ
অ,আ
ওষ্ঠ বর্ণ
উ,ঊ
তালব্য বর্ণ
ই,ঈ
কন্ঠতালব্য বর্ণ
এ,ঐ
উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি
☞ বর্ণ ও এর প্রকারভেদ
ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বা ধ্বনির লিখিত রুপকে বলা হয় বর্ণ অথবা ধ্বনিকে যখন আমরা লিখে প্রকাশ করি তখন সেটা হয়ে যায় বর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ ৫০টি।যেমন অ,আ, ক,খ । বর্ণ দুই প্রকার। যথা:- ১.স্বরবর্ণ ২.ব্যঞ্জনবর্ণ
স্বরবর্ণ: স্বরধ্বনি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত বর্ণ বা স্বরধ্বনির দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ১১ টি: হ্রস্ব স্বর ৪টি (অ, ই, উ, ঋ), দীর্ঘ স্বর ৭টি (হ্রস্ব স্বর বাদে বাকিগুলো)।স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হল ‘কার। কার আছে এমন স্বরবর্ণ ১০টি (শুধুমাত্র “অ” এর সংক্ষিপ্ত রূপ নেই)।
মৌলিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ৭টি: অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ২টি: ঐ = অ + ই, ঔ = অ + উ। অন্যান্য যৌগিক স্বরের কোন আলাদা বর্ণ নেই।
বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ২টি: ঐ = অ + ই, ঔ = অ + উ। অন্যান্য যৌগিক স্বরের কোন আলাদা বর্ণ নেই। বাংলা বর্ণমালায় মৌলিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ ৭টি: অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা
ব্যঞ্জনবর্ণ: ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি (প্রকৃত ৩৫টি + অপ্রকৃত ৪টি) । ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ হল ‘ফলা’। ফলা আছে এমন ব্যঞ্জণবর্ণ ৬টি: ম, ন, ব, য, র, ল ।
☞ মাত্রা কী এবং মাত্রা অনুযায়ী বর্ণের প্রকারভেদ
বর্ণের উপরে যে রেখা বা দাগ দেওয়া থাকে তাই মাত্রা । মাত্রা অনুযায়ী বাংলা বর্ণ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা:
পূর্ণমাত্রাযুক্ত বর্ণ: বর্ণের উপর পূর্ণ মাত্রা থাকে। পূর্ণমাত্রাযুক্ত বর্ণ ৩২ টি।এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৬টি ( অ,আ,ই,ঈ,উ,ঊ) এবং ব্যঞ্জণবর্ণ ২৬ টি।
অর্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ: বর্ণের উপর অর্ধেক মাত্রা থাকে। অর্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ ৮ টি। টি।এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১টি (ঋ) এবং ব্যঞ্জণবর্ণ ৭ টি (খ,গ,ণ,থ,ধ,প,শ)
মাত্রাহীন বর্ণ: বর্ণের উপর কোন মাত্রা থাকে না। মাত্রাহীন বর্ণ ১০ টি। টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ৪টি (এ.ঐ,ও,ঔ) এবং ব্যঞ্জণবর্ণ ৬টি (ঙ,ঞ,ৎ,ং,ঃ,ঁ)
☞ ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য
ধ্বনি শুধুমাত্র আমরা শুনতে পারি কিন্তু দেখতে পাই না । অন্যদিকে বর্ণ আমরা দেখতে পাই না।
ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগযন্ত্র দ্বারা কিন্তু বর্ণ শুধুমাত্র একটা চিত্র।
ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী যা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই শেষ।অপরদিকে বর্ণ দীর্ঘস্থায়ী যা লেখার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় না।
☞ বাংলা বর্ণমালা কাকে বলে
কোন ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার বর্ণমালা বলা হয়। যে বর্ণমালায় বাংলা বর্ণ লিখিত হয় তাকে বলা হয় বঙ্গলিপি বা বাংলা বর্ণমালা। বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ ৫০টি। স্বরবর্ণ ১১ টি ও ব্যঞ্জণবর্ণ ৩৯ টি ।
☞ বর্ণ ও অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য
ধ্বনিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যে চিত্র অংকন করা হয় তাই হল বর্ণ বা হরফ। । অপরদিকে অক্ষর হল এক বা স্বল্পতম প্রয়াসে বা নিঃশ্বাসে ( নিঃশ্বাসে বলা যুক্তিযুক্ত হবে না তবে শুধু বোঝার জন্য বললাম ) যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বলে। একে শব্দাংশ ও বলা যায়। ইংরেজি ভাষায় অক্ষরকে Syllable বলে। যেমন ‘বন্ধুর’ এখানে বর্ণ আছে ৫টি কিন্তু অক্ষর আছে মাত্র দুটি যথা একটা হল বন্ আরেকটা ধুর । অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে।
☞ স্পর্শধ্বনি ও এর প্রকারভেদ
ক থেকে ম পর্যন্ত মোট ২৫ টি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি (plosive) বা সৃষ্টধ্বনি ও বলা হয়। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এদেরকে পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হয়।
বর্গ
বর্ণ
উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
উচ্চারণের স্থান
ক-বর্গীয়
ক খ গ ঘ ঙ
কন্ঠ্য বা জিহবামূলীয় বর্ণ
জিহবার গোড়ালি ও তালুর নরম অংশের সহযোগে
চ-বর্গীয়
চ ছ জ ঝ ঞ শ য য়
তালব্য বর্ণ
দন্তমূলের শেষাংশ ও জিহবার সহযোগে
ট-বর্গীয়
ট ঠ ড ঢ ণ ষ ড় ঢ়
মূর্ধন্য বর্ণ
দন্তমূল ও জিহবার সম্মুখভাগ
ত-বর্গীয়
ত থ দ ধ ন
দন্ত্য বর্ণ
জিহবার ডগা আর দাঁতের উপর পাটির সংস্পর্শে
প-বর্গীয়
প ফ ব ভ ম
ওষ্ঠ্য বর্ণ
দুই ঠোঁটের সংস্পর্শে
স্পর্শধ্বনি
☞ উষ্মধ্বনি
এসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের কোথাও বাঁধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয়। উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি ৪টি: শ, ষ, স( অঘোষ অল্পপ্রাণ), হ ( ঘোষ মহাপ্রাণ )।
☞ অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি
এ ধ্বনি উচ্চারণের সময় নাক বা মুখ বা উভয় দিয়ে বাতাস বের হয়। নাসিক্য ধ্বনি বা বর্ণ ৫টি: ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। মূলত বর্গের পঞ্চম ধ্বনিগুলোই নাসিক্য ধ্বনি।
☞ অন্যান্য ধ্বনিসমূহ
অন্তঃস্থ ধ্বনি বা বর্ণ : এসব ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি। অন্তঃস্থ ধ্বনি ৪টি: ব, য, র, ল। এর মধ্যে আবার য তালব্য ধ্বনি, র কম্পনজাত ধ্বনি ও ল – কে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়।
পরাশ্রায়ী ধ্বনি বা বর্ণ ৩ টি : ং,ঃ, ৺ ( এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না।)
তাড়নজাত ধ্বনি: উচ্চারণের সময় দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার উল্টো পিঠের দ্বারা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে। তড়নজাত ধ্বনি ২টি: ড়, ঢ়।
অযোগবাহ ধ্বনি: এসব ধ্বনির স্বর ও ব্যঞ্জনের সাথে কোন যোগ নেই। অযোগবহ ধ্বনি ২টি: (ং, ঃ)।
খণ্ডব্যঞ্জণধ্বনি: ১টি(ৎ)।
নিলীন ধ্বনি : ১টি (অ)।
☞ অঘোষ ও ঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ
অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় বা ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর বেশি থাকে, তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। আর যে ধ্বনিগুলোতে বাতাসের জোর কম থাকে, নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাদেরকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। ক, গ, চ, জ- এগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি। আর খ, ঘ, ছ, ঝ- এগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি। অর্থাৎ বর্গের ১ম এবং ৩য় বর্ণ হলো অল্পপ্রাণ এবং বর্গের ২য় এবং ৪র্থ বর্ণ হলো মহাপ্রাণ ।
ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, অর্থাৎ গলার মাঝখানের উঁচু অংশে হাত দিলে কম্পন অনুভূত হয়, তাদেরকে ঘোষ ধ্বনি বলে। আর যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাদেরকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন, ক, খ, চ, ছ- এগুলো অঘোষ ধ্বনি। আর গ, ঘ, জ, ঝ- এগুলো ঘোষ ধ্বনি। অর্থাৎ বর্গের ১ম এবং ২য় বর্ণ হলো অঘোষ ধ্বনি বা বর্ণ এবং বর্গের ৩য় এবং ৪র্থ বর্ণ হলো ঘোষ ধ্বনি বা বর্ণ।
☞ অঘোষ ও ঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির বিচারে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ
ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ
অঘোষ ধ্বনি
ঘোষ ধ্বনি
অল্পপ্রাণ
মহাপ্রাণ
অল্পপ্রাণ
মহাপ্রাণ
নাসিক্য
ক
খ
গ
ঘ
ঙ
চ
ছ
জ
ঝ
ঞ
ট
ঠ
ড
ঢ
ণ
ত
থ
দ
ধ
ন
প
ফ
ব
ভ
ম
শ,ষ,স
হ
সংযুক্ত বর্ণের তালিকা
☞ সংযুক্ত বর্ণের তালিকা
সংযুক্ত বর্ণ
উদাহরণ
ক্ত = ক্+ত
শক্ত
ক্র=ক্+র
চক্রান্ত
ক্ষ=ক্+ষ
বক্ষ
ঙ্ক= ঙ্+ক
অঙ্ক
ঙ্গ = ঙ্+গ
অঙ্গ
জ্ঞ= জ্ + ঞ
জ্ঞান
ঞ্ছ= ঞ+ছ
বাঞ্ছিত
ঞ্জ = ঞ+জ
গঞ্জ
ঞ্চ= ঞ্+চ
সঞ্চয়
ট্ট=ট্+ট
অট্টালিকা
ত্ত= ত্+ত
উত্তম
ত্+থ
উত্থান
দ্ধ= দ্+ ধ
বদ্ধ
ব্ধ = ব্ + ধ
লব্ধ
হ্ম = হ্ +ম
ব্রহ্মা
ক্ষ্ম = ক+ষ+ম
লক্ষ্নী
হ্ন=হ্+ন
মধ্যাহ্ন
হ্ণ=হ্+ণ
পূর্বাহ্ণ
হৃ=হ্+ঋ
হৃদয়
হু=হ্+ উ
হুকুম
ষ্ম= ষ্+ম
গ্রীষ্ম
ণ্ড = ণ্+ড
কাণ্ড
রূ = র্ + ঊ
রূপ
ষ্ঞ = ষ+ণ
তৃষ্ঞা
🏷️ Category
ধ্বনি, বর্ণ ও বাগযন্ত্র
🎓 Course
পল্লী বিদ্যুৎ জব প্রিপারেশন কোর্স
❓ MCQ Questions
-
Q: কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?
A. চ ছB. ড ঢC. ব ভD. দ ধ✔ Correct Answer: A
-
Q: নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
A. ভB. ঠC. ফD. চ✔ Correct Answer: A
-
Q: ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
A. আজি-আইজB. পিশাচ-পিচাশC. পাকা-পাক্কাD. স্কুল-ইস্কুল✔ Correct Answer: B
-
Q: তাড়নজাত ধ্বনি কোনটি?
A. শB. রC. ড়D. স✔ Correct Answer: C
-
Q: যে ছন্দে যুক্তধ্বনি সব সময় একমাত্রা হিসেবে গণনা করা হয় তাকে কি ধরনের ছন্দ বলে?
A. মাত্রাবৃত্ত ছন্দB. অক্ষরবৃত্ত ছন্দC. স্বরবৃত্তছন্দD. পয়ার ছন্দ✔ Correct Answer: B
-
Q: বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?
A. ৭ টিB. ৯টিC. ১১ টিD. ১৩ টি✔ Correct Answer: A
-
Q: এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলে-
A. শব্দB. বর্ণC. বাক্যD. অক্ষর✔ Correct Answer: D
-
Q: 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি?
A. যৌগিক স্বরধ্বনিB. তালব্য স্বরধ্বনিC. মিলিত স্বরধ্বনিD. কোনোটি নয়✔ Correct Answer: A
-
Q: বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি?
A. তৃতীয় বর্ণB. দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণC. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণD. দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ✔ Correct Answer: B
-
Q: মুহাম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?
A. বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানB. আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানC. ধ্বনিবিজ্ঞানের কথাD. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব✔ Correct Answer: D
📝 Written Questions
No written questions selected.